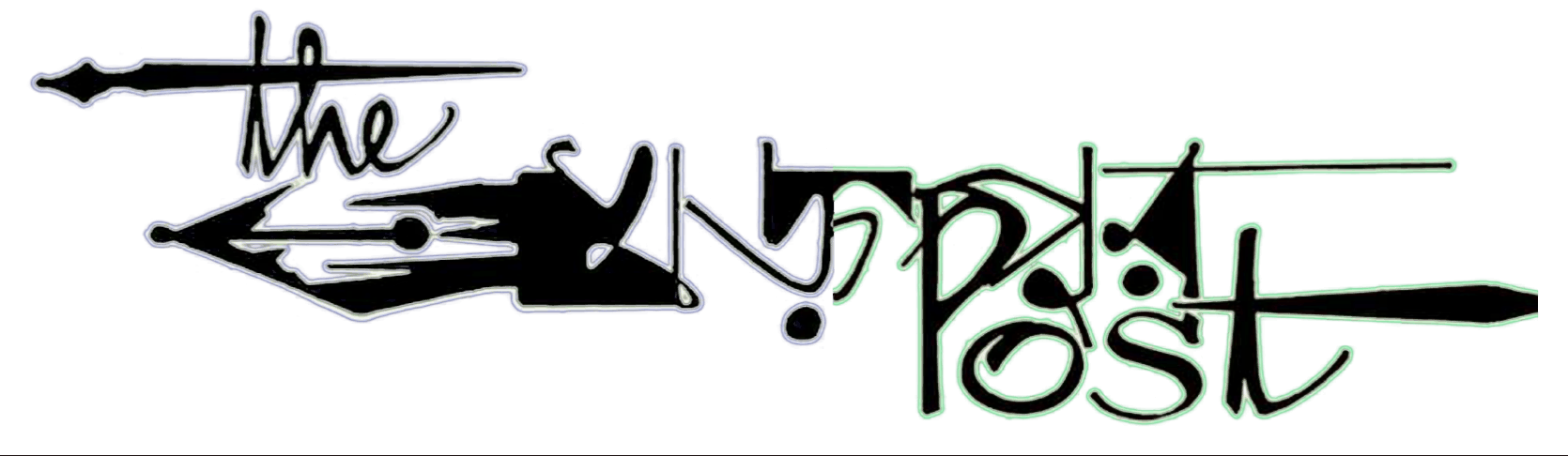ঈশ্বর গুপ্ত, নব যুগের কবিয়াল বিনোদ মন্ডল
উনিশ শতকের শুরুতে বাংলা তথা ভারতবর্ষের বুকে মধ্যযুগের নানা উপসর্গ যখন বিলীয়মান হতে শুরু করেছে এবং নতুন যুগের সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সেই যুগসংঘাতের মধ্যে আবির্ভূত (১৮১২—১.৮.১৮৫৯) হয়েছেন। স্বভাবতই তাঁর ৪৭ বছরের জীবন জুড়ে সেই কালের টানাপোড়েন তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করেছে বারংবার।
বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে সম্ভ্রমের সাথে একালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে লিখেছিলেন, ‘কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরো গুরুতর লাভ।’ কোম্পানির কাছে আত্মসমর্পিত জাতি যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা হারিয়ে বেপথু, তখন রামমোহন সামাজিক ও নৈতিক জীবনে দেশকে দিশা দেখাতে অবতীর্ণ হন। অন্যদিকে সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নেতা রূপে ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের অনিবার্য উপস্থিতি সমাজকে আলোড়িত করেছে।
কলকাতা থেকে ৩০ মাইল উত্তরে ভাগীরথীর পূর্বপাড়ে সেকালের কাঞ্চনপল্লী, একালে যা কাঁচড়াপাড়া নামে খ্যাত, সেখানেই ঈশ্বরের জন্ম। বাবা হরিনারায়ণ, মা শ্রীমতী দেবী। তবে বাল্যকাল থেকে ঈশ্বর কলকাতায় জোড়াসাঁকোতে মামাবাড়িতে কাটিয়েছেন। ডানপিটে স্বভাবের ছিলেন। তাই পুঁথির পাতা তাকে কখনও আকর্ষণ করেনি বরং প্রান্তরের ঝরাপাতা, শস্যের শ্যামল শোভা, নদীর কলতান আর সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে তাঁর মনের মণিকোঠায় এক স্বভাব কবি পাখা মেলেছে। মুখে মুখে অনর্গল ছড়া কাটতেন। যাকে সামনে পেতেন তাকেই শোনাতেন। এই অভ্যাস শেষ জীবনেও অটুট ছিল। পারিবারিক কিছু বিপর্যয় তাকে কৈশোরেই বিধ্বস্ত করে। মাতৃ বিয়োগ, বাবার পুনরায় পাণি গ্রহণ, অপছন্দের পাত্রীর সঙ্গে বিয়ে, পছন্দের মানসপ্রতিমাকে বিয়ে করতে না পারা, এই ঘটনাক্রম তাঁর মানসপ্রকৃতিকে হতাশা,দ্বন্দ্ব, তীর্যক সন্দেহে কঠিন করে দিয়েছিল। স্বভাবতই তিনিও সেই আবর্ত থেকে বের হতে পারেননি। জীবনকে বাঁকা চোখে পরখ করেছেন, মাতৃজাতিকে ব্যঙ্গের বর্শা ফলকে বিকৃত করে এঁকেছেন। তবে কলকাতায় যোগেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে আপাত ভবঘুরে ছেলেটি ইতিবাচক জীবনে সৃষ্টি ও সংগ্রামে উন্মুখর হতে পেরেছেন শেষে।
তেমন প্রথাগত শিক্ষা না থাকলেও এই প্রতিভাধর মানুষটি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রেখেছেন। তাঁর প্রধান কাজ সাপ্তাহিক সংবাদ প্রভাকর প্রকাশ(২৮.১.১৮৩১ প্রথম প্রকাশ)। ১০.৮.১৮৩৬ থেকে যা সপ্তাহে তিন দিন এবং ১৪.৬.১৮৩৯ থেকে দৈনিক পত্রিকা রূপে পথ চলা শুরু করে। এটাই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। অচিরেই পত্রিকাকে ঘিরে একদল প্রতিভাধর কবি লেখক সাহিত্য অঙ্গনে ধারাবাহিক কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। আজ তাঁদের অনেকেই স্বনামধন্য। রঙ্গলাল, দিনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রগণ্য। এছাড়াও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেন্দ্র নাথ ঠাকুর, অক্ষয় কুমার দত্ত, মনোমোহন বসু, রাধাকান্ত দেব, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর সংবাদ প্রভাকরের পরিবারভুক্ত ছিলেন। এই কাগজ যেমন বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার নানা স্বাক্ষর বহন করে, তেমনই হারিয়ে যাওয়া নানা গ্রামীণ কবিয়াল ও শিল্পীর গান ও জীবনী প্রকাশ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। রামপ্রসাদ, নিধুবাবু, রাম বসু, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, কেষ্টা মুচী, লালু নন্দলাল এবং হরু ঠাকুরগণ সেকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁরা সংবাদ প্রভাকরের মাধ্যমে ইতিহাসে ঠাঁই পেয়েছেন, যশস্বী হয়েছেন।
ঈশ্বর গুপ্ত যেহেতু সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় হোলটাইমার ছিলেন, স্বভাবতই ঘটনাচক্রে আরও তিনটি পত্রিকা সম্পাদনার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। সেগুলি হল- সংবাদ রত্নাবলী (সাপ্তাহিক), পাষণ্ডপীড়ন এবং সংবাদ সাধুরঞ্জন। কলকাতার ধনাঢ্য সমাজ এগুলি প্রকাশনায় অর্থ সরবরাহ করেছেন। তবে এসবই কাল ক্রমে বন্ধ হয়ে গেছে। সংবাদ প্রভাকরের খিদে মেটাতে গিয়ে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা ও গদ্য রচনাগুলি মুদ্রণের মুখ দেখেছে। সাংবাদিক হিসেবে খবর ও নিবন্ধ রচনা ছাড়াও তিনি মহাকালের হাতে নিম্ন বর্ণিত গ্রন্থ গুলি অঞ্জলি দিয়েছেন।
১/ কালী কীর্তন (১৮৩৩)
২/ কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত (১৮৫৫)
৩/ প্রবোধ প্রভাকর (১৮৫৮)
৪/ হিত-প্রভাকর (১৮৬১)
৫/ স্বরচিত কবিতাবলীর সারসংগ্রহ (১৮৬২)
৬/ বোধেন্দু বিকাস ( সংস্কৃত নাটকের ভাবানুবাদ/১৮৬৩)
ঈশ্বরগুপ্ত সেকালের কলকাতায় যথেষ্ট পরিচিত ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন। উপরিউক্ত গ্রন্থ গুলির মধ্যে প্রথম তিনটি তাঁর জীবদ্দশায় এবং বাকিগুলি মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তাঁর সমকালে অন্য সম্পাদকের সম্পাদনায় তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি হল-
১/ লেখকগণের প্রতি উপদেশ (১৮১১)
২/ আম্র (১৮১২)
৩/ গোল আলুর গর্ব (১৮১২)
৪/বাল্য বিবাহ (১৮১৩)
একালে সাহিত্যের হোলটাইমার অনেক দেখা যায়, যাঁরা মূলত কলমজীবী। তাঁদের অধিকাংশ নীরবে সৃষ্টিতে ব্যস্ত থাকেন। সভা সমিতিতে জনসমক্ষে তেমন একটা যাতায়াত করেন না। আবার কেউ কেউ সামাজিক কারণে পরিচিতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাধ্যমত জনসংযোগ করেন। সভা সমিতিতে যান। সাহিত্য সভা/সম্মেলনে সভাপতি/অতিথির আসন অলংকৃত করেন। ঈশ্বরগুপ্ত শেষোক্ত পর্যায়ের প্রতিনিধি শুধু নন, অগ্রগামী পদাতিক। তিনি তত্ত্ববোধিনী সভা, নীতি তরঙ্গিনী সভা, দর্জিপাড়ার নীতি সভা প্রভৃতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে কবিতা প্রবন্ধ পাঠ করতেন, বক্তব্য রাখতেন। ভাবতে অবাক লাগে আজকের দিনে যে অসংখ্য সাহিত্য বাসর অনুষ্ঠিত হয়, বাংলায় তিনিই প্রথম চালু করেন। কলকাতার পটলডাঙ্গার প্রভাকর পত্রিকার দপ্তরে ( ইংরেজি ১৮৫০) ১২৫৭ বঙ্গাব্দের নববর্ষ থেকে প্রতিবছর সাহিত্য সভার আয়োজন করতেন। শুধু তাই নয়, সেইসব বাসরে আমন্ত্রিত সেকালের সম্ভ্রান্ত বাবু জমিদারগণ উৎকৃষ্ট রচনা স্রষ্টাকে উৎসাহিত করতে নগদ অর্থ পুরস্কার দিতেন এবং এসব তাৎক্ষণিক হতো না, ঈশ্বর গুপ্ত রীতিমতো পরিকল্পনামাফিক দাতা ও গ্রহীতার কর্মসূচি নির্ধারণ করতেন। সুপুরুষ, সুদর্শন এই মানুষটি রক্ত সূত্রে কবিয়াল ছিলেন। সুরুচি ও শিক্ষার অভাবে সব লেখায় প্রসাদগুণ বিকশিত হয় নি। কিন্তু সহজ সরল রসময় ভাষায় তিনি প্রথম তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়কে কাব্য মর্যাদায় উত্তীর্ণ করেন।
অন্তরে দোলাচল ছিল। ফলে কবি ও সাংবাদিক হিসেবে সব সময় বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক অবস্থান গ্রহণ করতে পারেননি। এসব নিয়ে, তাঁর সাহিত্য কর্ম নিয়ে, বহু আলোচনা হয়েছে, তাই সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। তবে আধুনিক গবেষকগণ নানা তথ্য দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন, সিপাহী বিদ্রোহের আগে তিনিই প্রথম স্বাদেশিকতা, স্বাধীনতা, জাতীয়তাবোধ প্রভৃতি নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন। আধুনিকতার নামে, ইংরেজিয়ানার নামে, বাঙালিয়ানাকে অবহেলা তিনি মানতে পারেননি।
পরিশেষে বলি, নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই প্রথম বাঙালি কবি, যাঁর কবিতায় স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্রবোধ বাণীরূপ লাভ করেছিল সবার আগে। ‘মাতৃভাষা’, ‘স্বদেশ’, ‘ভারতের অবস্থা’, ‘ভারতের ভাগ্যবিপ্লব’, ‘অনাচার’ প্রভৃতি কবিতা তাঁর উজ্জ্বল নিদর্শন। অসমসাহসী এই কবিয়াল ‘অনাচার’ কবিতায় সরাসরি ইংরেজ কোম্পানিকে অভিযুক্ত করে লিখেছেন-
“ওহে কাল কালরূপ করালবদন।
তোমার বদনযুক্ত মরাল বাহন।।
দেবদেবী কত তুমি করিয়া সংহার। ভারতের স্বাধীনতা করিলে আহার।।